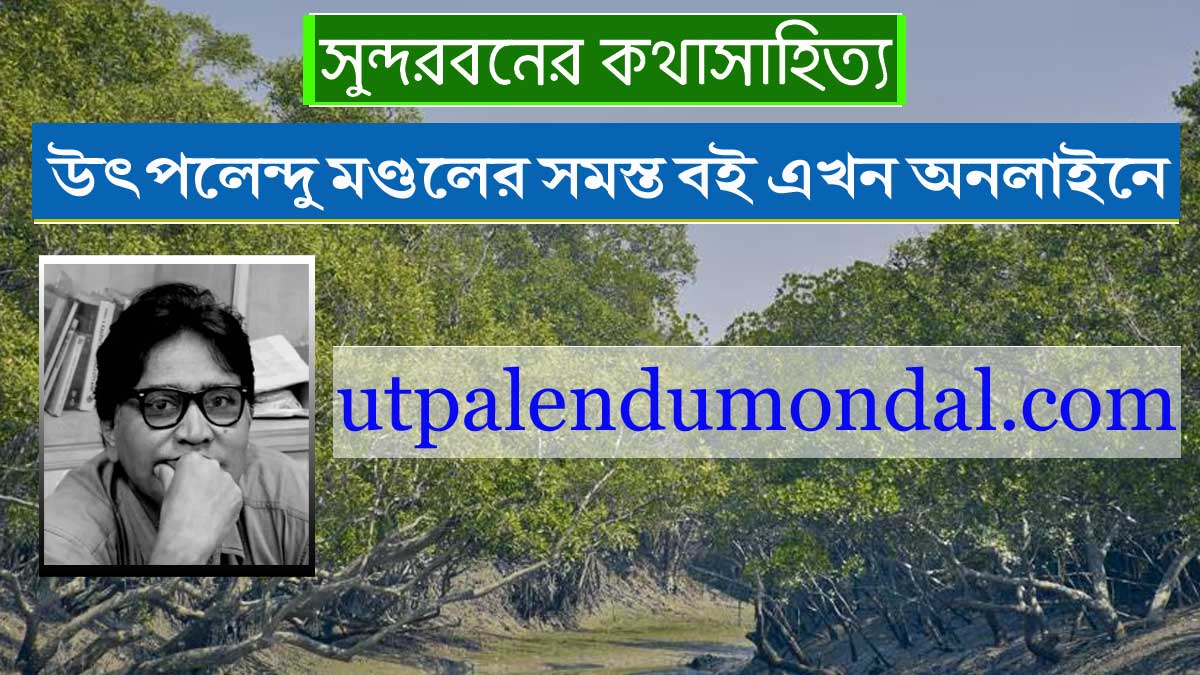ইতিহাস ও সাহিত্যের আলোকে প্রান্তিক মানুষের শোষণ, প্রতিরোধ ও সংস্কৃতির চিত্র। আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব থেকে আধুনিক যুক্তিবাদী চেতনা পর্যন্ত দলিত জীবনের লড়াই এবং সুন্দরবনকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা নিয়ে লিখলেন অপরেশ মণ্ডল
এক

একদল উচ্চবংশবর্গী, রাজ ক্ষমতায় বলীয়ান, সুবিধাভোগী, অর্থের জোরে স্বঘোষিত সমাজপতিদের দ্বারা আর্থিক ভাবে দুর্বল, সামাজিক অনগ্রসর, শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত জনগনের দলন, পীড়ন, বঞ্চনার শিকার হওয়াকে ‘দলিত’ হওয়া বোঝায়। এককথায়, এই ব্যবস্থা শোষক ও শোষিত পরম্পরার আলো-আঁধারীর ইতিবৃত্ত। আর্যদের ভারত আক্রমণের পর পরাজিত মূলনিবাসী বহুজন মানুষেরাই চরম বর্ণ বৈষম্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। তারাই দলিত। আমরা তথাকথিত হিন্দু বর্গভুক্ত মানুষ সেই কোন সুদূর অতীত থেকে আমাদের আত্মপরিচয় অন্বেষণ করে ফিরছি। এই তো কয়েকযুগ আগেই, এ দেশীয় মানুষ, বৈদিক যুগ থেকে বর্ণ বৈষম্যের শিকার হতে হতে, সামাজিক সাম্যের অধিকার বঞ্চিত হয়ে অম্বেডকর প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধান মোতাবেক তপশিলি জাতি হিসেবে শিক্ষা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষের অধিকারে বাঁচার সংরক্ষণ পেয়েছে। নইলে ব্রাহ্মণদের শোষণ থেকে মুক্তি এখনও বহুত দূর। আমরা জেনেছি ‘অসুর দলনী দেবী দুর্গা’ কিংবা ‘মহিষাসুর মর্দিনী’ বাক্যবন্ধ। এই ‘দলনী’ ও ‘মর্দিনী’ শব্দের ভেতর অসুর শ্রেণির প্রতি মারাত্মক বিদ্বেষ ভরে দিয়েছেন শাস্ত্রকাররা। অসুর এখানে অশুভের প্রতীক, সে মন্দ কুৎসিত। অথচ ঋগ্বেদে অসুর শব্দ শুভ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটা বিশেষ শ্রেণির মানুষকে বা বলা ভালো যুদ্ধে পরাজিত অসুর জাতির রাজাকে হত্যা করে বিজয় উৎসব পালন করার প্রতীক দুর্গা পুজো। মহান অসুর সম্রাট মহীয়স অসুরকে একজন নারী কর্তৃক অসহায় হত্যা হওয়ার দৃশ্যকে অবলম্বন করে পুতুল পুজো খুবই বেদনাদায়ক। আমরা জানি আর্য আগমনের পূর্বে অসুররা এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ভারতে। প্রাচীন যুগে অ্যাসুরিয় সভ্যতা তার প্রমাণ। অসুররা নারীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। এই দুর্বলতা দেবতাদের অজানা ছিলনা। ফলে নিজের জীবন দিয়েও মহীয়স তাঁর ক্ষাত্রধর্ম রক্ষা করেছিলেন।
আর্য আর অনার্যের যুদ্ধ আসলে মূল ভারতীয় সংস্কৃতি বনাম বহিরাগত সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব সংঘাত সম্ভুত। এটাকেই বহিরাগত বর্বররা দেবতা আর অসুরের সংগে তুলনা করে অসুরদের ওপর দেবতাদের কর্তৃত্বের আখ্যান নির্মাণ করেছেন। বেদ, পুরাণ ও মহাকাব্যে ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। এই স্বঘোষিত শ্রেষ্ঠত্বকে যুক্তিবাদী বৌদ্ধরা মানেনি। অর্থাৎ মূল ভারতীয় যারা বহিরাগত আর্যদের কতৃত্ব মানেনি বা তাদের সংস্কৃতি, ভাষা গ্রহণ করেনি তারা অভিহিত হলো দাস, দস্যু, দৈত্য, রাক্ষস, দানব ইত্যাদি অপমানসূচক অভিধায়। তাঁরাই আর্য ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থায় পরিচিত হলেন পতিত বা অতিশূদ্র হিসেবে। আর যারা বৈদিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হল বা শাসকের বশ্যতা স্বীকার করল তাদের স্থান হল সমাজের একদম শেষের সারিতে। তারা হল শূদ্র। তাদের কাজ হল বাকি তিন উচ্চবর্ণের সেবা করা। আর পতিত বা অচ্ছুতদের সম্পত্তির অধিকার থাকল না, শিক্ষার অধিকারও হারালো । কেবল প্রভুর উচ্ছিষ্টান্নই তাদের আহার। এরই নাম দলন আর এই মানুষেরাই হল দলিত। প্রান্তজনসমাজের পিছিয়ে রাখা মানুষমাত্রই দলিত। বর্তমানে দলিত বলতে কেবল তপশিলি জাতি / উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিকে বোঝানো হয়। স্থান, কালভেদে দলিতমানুষের সামাজিক অবস্থান অনেকটাই বদলেছে। এখন দলিত দলনের, নিষ্পেষণের ছবিটা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের আধারে পরিপুষ্ট হচ্ছে। জল চল ও জল অচলের বিভেদটা আজও বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে সামাজিক বৈবাহিক সম্পর্কেও।
দুই

সুন্দরবন মানব দ্বীপবসতির অন্দরে সেই অতীতের অনুরণন ও ছায়াপাত দেখতে পাই। এখানেও রয়েছে সেই ঘৃণ্য জাতিভেদ। রয়েছে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা আর আছে পাল্টা প্রতিরোধ, দ্রোহ। চোখে চোখ রেখে শোষক তথা দলনকারীদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আগুন। সুন্দরবনে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে জংগলাকীর্ণ নদীদ্বীপ আবাদ করে জনবসতি গড়ে ওঠে। জমিদার ছিল ব্রিটিশ কোম্পানী অথবা দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায়। কায়স্থরা আসলে জলচল শূদ্র। এরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিপোষক। আর জল অচল শূদ্ররা পতিত, অচ্ছুত। এরাই দাস, দস্যু, চণ্ডাল ইত্যাদি অপরাধ প্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরাই একদা জঙ্গলমহলে জল-জঙ্গল-জমিনের স্বাভাবিক অধিকারী ছিল। অথচ সেই মানুষেরাই অভাবের দায়ে মাতৃসমা সুন্দরবনের জংগলকেই হাসিল করতে বাধ্য হয়েছিল। রাঁচি, সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগনা তাদের আদিনিবাস। কারণ ব্রিটিশরা ততদিনে তাদের আবাসভূমির অধিকারে থাবা বাড়িয়েছে। তার পরিণামে সাঁওতাল হুল বিদ্রোহে (১৮৫৫) সিধো কানহু, মুণ্ডা বিদ্রোহ তথা উলগুলানে (১৮৯৯-১৯০০) প্রাণ বলিদান দিয়েছেন বীরসা মুণ্ডা। সেই প্রতিবাদী তথাকথিত অতিশূদ্র ও পতিত আদিবাসীদের দ্বারা দুর্গম জঙ্গল হাসিল করে কি জমিদাররা তাদের বিদ্রোহকে পরিহাস করল? আড়কাঠি বা দালাল মারফত তাদের আগমন ঘটে নোনাদেশেরই বিভিন্ন আবাদি দ্বীপে। তারা ছিল প্রকৃতই সুন্দরবনের মাটির মানুষ। তাদের সন্ততিরাই সুন্দরবনের ভূমিপুত্র।
তিন

নবগঠিত সুন্দরবনের সমাজ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ছিল সেই ব্রাহ্মণ ও তাদের প্রবর্তিত পৌরাণিক মনুবাদী অনুশাসন। এই আইনের সার্থক রুপায়ণ ঘটাতে অবস্থাপন্ন শূদ্র জোতদার, গাঁতিদার, চকদার ও মহাজনরাই সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন । তাঁরাই সমাজের হত্তাকত্তা। গ্রামের বিচার-শালিসিতে তাঁরা যা নিদান দেবেন সেটাই শিরোধার্য! নইলে একঘরে হওয়া কিংবা ধোপা-নাপিত বন্ধ হওয়ার বালাই অবধারিত। এমনকি পানীয় জলটুকু পাওয়ার উপায় থাকত না। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত হিন্দু বিবাহ আইন (১৮৫৬) লাগু হওয়ার অনেক আগে থেকে আদিবাসী সমাজে বিধবাবিবাহ চালু ছিল। সুন্দরবনের পৌণ্ড্র, নমশূদ্র, বাগদী, রাজবংশী, জেলে, মালো, তিওর সমাজেও ধীরেধীরে নানান সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ হয়। ক্রমে গুরুবাদী ব্যবস্থার আগমন। ভয় ও ভক্তিতে গরীব সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ পরকালের সুন্দর জীবনের কামনায় তাদের ইহকাল গুরুসেবায় সঁপে দিত। এই সুযোগে গুরু ঠাকুররা শিষ্যবাড়ি থেকে বৎসরান্তে চাল, সম্মান দক্ষিণা নিয়ে হৃষ্ট মনে ঘরে ফিরতেন। ব্যবসাটা মন্দ নয়। গরিবের অন্ন না জুটলেও পরকালের সুখপিয়াসী মানুষ বুকে পাথরচাপা দিয়ে চোখের অশ্রু ভাব সাগরে ভাসিয়ে ‘গুরু কৃপাহি কেবলম’ জপত। এভাবেই গরিবকে শোষণ করে ব্রাহ্মণরা। এই প্রথা বিগত কুড়ি বছরে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়েছে বলা যায়। আজকাল লোটাকম্বল সর্বস্ব সেইসব গুরু ঠাকুররা সময়ের ধারাস্রোতে ভেসে গেছে। মানুষ আবার প্রকৃতির কাছে ফিরতে চায়। প্রান্তবাসী মানুষ লেখাপড়া শিখে অতীত অনুশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। এখানেই যুক্তিবাদী চেতনার জয়। সুন্দরবন কিন্তু জাগছে।
চার

সুন্দরবনের কথাসাহিত্য প্রথম দিকে সুন্দরবনকেন্দ্রিক। বিশ শতকের তিন চারের দশকে শুরু হয় সুন্দরবনকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের জয়যাত্রা। তার আগে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকরা সুন্দরবনের কথা লিখেছেন রুপক ও রম্যরসের আড়ালে। তিনের দশকের মাঝামাঝি থেকে বামপন্থী ভাবধারার কিছু নেতৃস্থানীয় তাত্ত্বিক নেতারা গর্জে ওঠেন জমিদারের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। তাঁরা কেউ সুন্দরবনের ভূমিপুত্র কেউবা আবার দলের ঊর্ধ্বতন নেতার নির্দেশে সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন সুন্দরবনের দরিদ্র শোষিত অধিকার বঞ্চিত দলিত মানুষকে নিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। সেই ধারায় সর্বাগ্রগণ্য জননেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরিন্দম নাথ, গজেন মাইতি, সেবক দাস, হেমন্ত ঘোষাল, ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, প্রশান্ত শূর প্রমুখ। তাঁদের স্মৃতিকথায় সুন্দরবনের দলিত মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও দ্রোহের আখ্যান উঠে এসেছে। পরে পাঁচের দশকে লিখছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শিবশংকর মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সাত আটের দশকে সুন্দরবনের ভূমিপুত্র লেখক উৎপলেন্দু মণ্ডল, সন্তোষ বর্মন, প্রসাদ মণ্ডল, প্রমোদ পুরকাইত, প্রদীপকুমার বর্মন, হেদায়েতুল্লাহ, সোহারাব হোসেন, পূর্ণেন্দু ঘোষ প্রমুখের গল্পে উঠে আসছে সুন্দরবনের দলিত মানুষের জীবন ও দ্রোহের নানান আখ্যান। লোকাচার, জীবিকা ও জাতপাতদীর্ণ সমাজের ভাঙাগড়া কিছুই বাদ গেল না তাঁদের লেখনি থেকে। নয়ের দশকের কল্যাণ মণ্ডল, বিকাশকান্তি মিদ্যা লিখছেন সুন্দরবনের আকাঁড়া জীবনের যন্ত্রণার কথালিপি। একুশের প্রথম দশকে আসছেন সুশান্ত পাত্র, সুব্রত মণ্ডল, পবিত্র মণ্ডল প্রমুখ। বর্তমানে দলিত সাহিত্যের আঙিনায় সুন্দরবনের প্রান্তজনের সাহিত্য তাঁদের হাতে বেশ সংগঠিতভাবে চর্চার পরিসর পেয়েছে।
ছবি: উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়