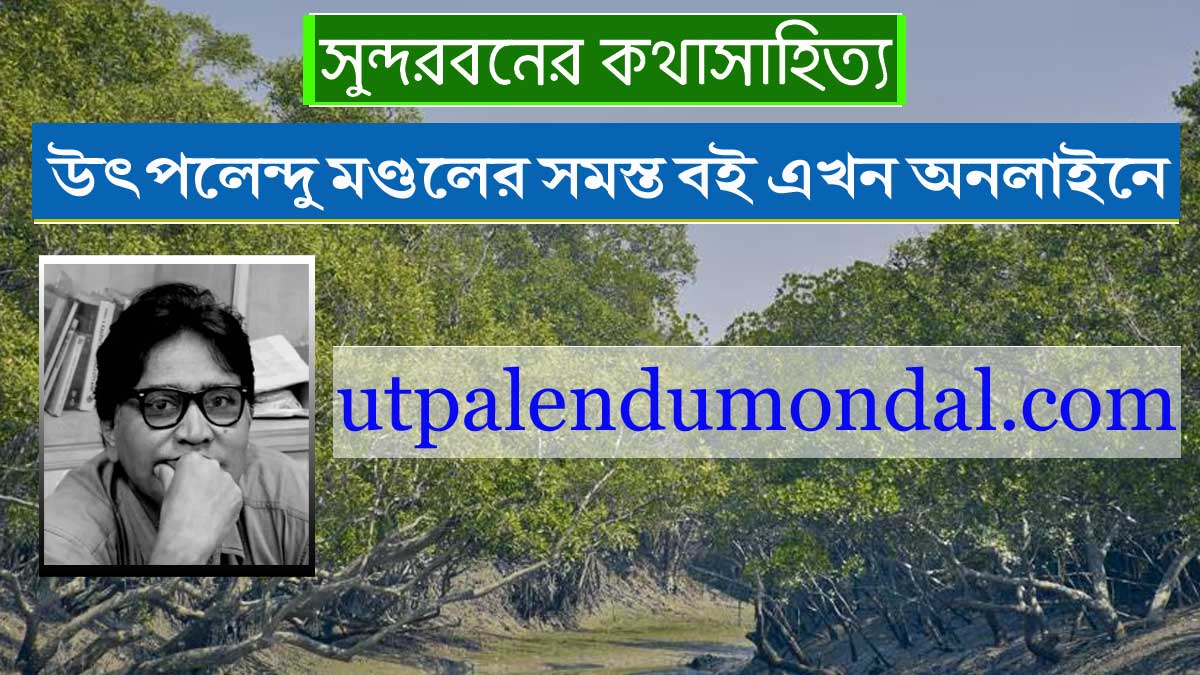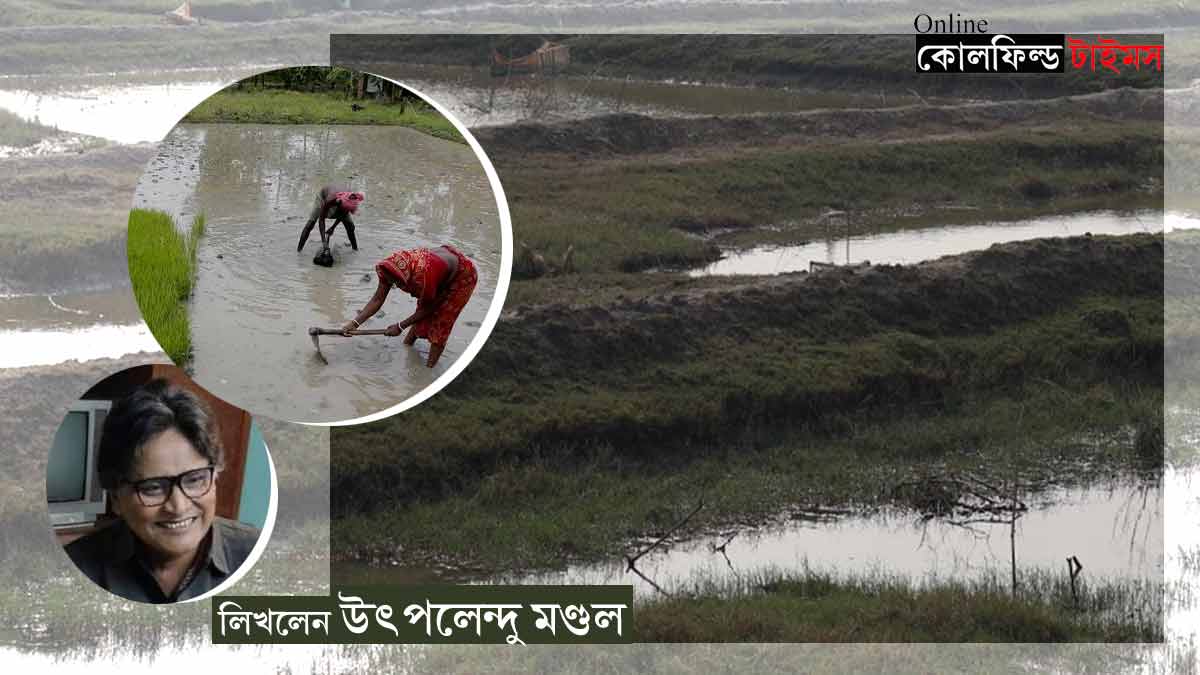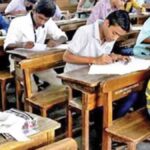উৎপলেন্দু মণ্ডল
তখন ছিল দু’মুখো সময়। আশ্বিন-কার্তিক মল মাস। মাঠে ফলন্ত ধান অথচ ঘরে চাল বাড়ন্ত, একবেলা খাওয়া। সকালে গৃহস্থ বাড়ির পুকুর-উঠোন পেরিয়ে কানা হরি আসত আমাদের দরজার সামনে। চুপচাপ বসে থাকত। মাঝে মাঝে পান্তা ভাতের জন্য বসে থাকা, ভাত যদি না হয় শুধু পান্তার ঝোল। কয়েকবছর আগেও চোখে দেখতে পেত, প্রথমে হয়েছিল রাত কানা। গ্রামে-ঘরে অমন কতই হয়। পরে একেবারে কানা অন্ধ।
আর কয়েক মাস পরে আমাদের ধান পাকলো, নাবাল জমিতে সেবার সাদামাটা ধান খুব ফলল। আমাদের ওখানে তখনও আসেনি উচ্চ ফলনশীল ধান। আরও কয়েক দশক পরের কথা, তখন হরির ভগ্নিপতি আমাদের নাবাল জমিতে কয়েকদিন আগে গোড়া দিয়ে গেছে, আজ মাথাল দিয়ে গেছে। পরে মাথামোটে উঠোনে তুলবে। বিকেলের রোদ ওম ছড়াচ্ছিল। সদানন্দর কাঁদায় গরু চরছে। আর কদিন পরে গোরু ব্যেকম দেবে। তখন আর গোরুর রাখাল লাগবে না।এ বার কী এক পোকা এসেছে ধানের পাপড়ি কেটে দিচ্ছে। আমি এক মনে ধানের পাপড়ি তুলছিলাম, হঠাৎ দেখি পঞ্চানন আর হরি মারামারি করছে। আমাদের কিছুটা দূরে শান্তি খালের ওপারে কিষেনরা কাজ করছিল, ওরা হাঁকাহাঁকি করে । আমি কাছে আসতেই হরি কাচিটা দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়। আমি ওর ঘাড় ধরে নিয়ে যাই। হরি তখনও রাগে কোঁদ-কোঁদ করছে। এর মধ্যে আমি ওকে খুব বকি, চিৎকার কার করে বলে , নাগ না চন্ডাল। জিজ্ঞেস করলাম কাস্তে ফেলে দিলি কেন তুই?
তখন বলে, নাগ না চন্ডাল। তা তো ঠিক ঠিকই বলেছে হাজার হোক হরির জামাইবাবু। অবশ্য বউয়ের পয়সায় খায়, ওর বউ কালী দীর্ঘাঙ্গি, গ্রামাঞ্চলে এরকম চেহারা বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের গোবর গাদায় গোবর ফুরণ নিতো। গোবর চটকে তাল তাল বানিয়ে ঘুটে বানাতো। পরে কলকাতা যাওয়ার হিড়িক পড়ল। তখন কালী কলকাতায় গিয়েছিল আর ফেরেনি। কালীর আরেক ভাই ছোট ছিল। এখন লম্বা-চওড়া মরদ। বাড়ি করেছে সরকারি দাক্ষিণ্যে। কিন্তু হরি আর নেই। সে কলকাতায় যায়নি। আমাদের ডাউন দেশে সে দেহ রাখল।
আমাদের একদা ধান খেত এখন অন্য লোকের। সেখানে এখনো ধান চাষ হয় ,কিন্তু সার, ওষুধ এ সব লাগে। আগে খোয়ালি করার সময় হতো না। লোকের তাতেও ভালো ধান হতো। কিন্তু এখন সবাই খোওয়ালি করে, সে সময়ে ধান গাছের মাঝখানে প্রচুর শ্যাওলা জমত। ধান কাটার সময় সেই শ্যাওলা শুকিয়ে মাটির সঙ্গে একেবারে লেপটে যেত। ভারী সুন্দর এক গন্ধ। তার নিচে ধানি কাঁকড়া, ধানি কেউটে, কচ্ছপ আশ্রয় নিত। ধান গোড়া দেওয়ার সময় মাঝে মাঝে কচ্ছপও পেত।
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আদিবাসীরা বিশেষত মেয়েরা ধান ক্ষেতে ঢুকে পড়ত। মাথায় থাকতো চকচকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি। আমরা নেংটা ভুতুমরা ছড়া কেটে বলতাম, বুনো মাগি কুটকুট, দুপয়সার বিস্কুট। বিস্কুট তখনও মহার্ঘ।প্যাকেটও আসেনি বিস্কুট আসত টিনের কৌটোয়। তাও ভাঙাচোরা বিক্রি করার লোকরা নিয়ে আসত। ওজনে বিস্কুট দিত। নদীময় সুন্দরবনে প্রত্যেক লঞ্চে পাওয়া যেত। তারা এক ধরনের লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চা খেত। সে চা সুন্দরবনের জলের মতো নোনা। পরে স্থানীয় লোকরা মানে সুন্দরবনীরা যখন চা খাওয়া শুরু করল তখন চায়ের গুড়োর মতো সার কিংবা বিষও খেতে শুরু করল। দু-একজন তাতে উপরে চলে গেল। বাকি যারা থাকল তারাও পগার পার। এখন তারা অন্ধ কিংবা তামিলনাড়ুতে না হলে কেরলেও চলে যায়। চাষের সময় জমি পড়ে থাকে। কিষান পাওয়া যায় না। ওরা দক্ষিণ থেকে এসে দু-একদিন থাকে। বীজ বপন করে আবার দক্ষিণ ভারতে চলে যায়।
সে কারণেই এখানকার নাবাল জমি এখন জোয়ারের জলে মাছ চাষ। নদীর মাছ ভেড়িতে তোলে স্থানীয়রা। বেপারী আসে প্রায় প্রত্যেকদিন,মুখে একশো বিশ জর্দা, গলার কাছে তুলসীর মালা,তারা মাছ চালান দেয় কলকাতায়। আগে যেত লঞ্চে, এখন বাসে। প্রত্যেকটা নদীতে প্রায় ব্রিজ হয়ে গেছে। ইকো সিস্টেম বরবাদ। লোক এখন শহর নেশায়। গ্ৰামে আসে অবসরযাপন কিংবা অক্সিজেন নিতে। গ্রাম গ্রামেই আছে, মাঝখান থেকে গ্রামের নিজস্ব ইকোসিস্টেম চলে গেল। চলে গেল গ্রামের আচারবিচার। এক ভুবন গ্রামের আদর্শ গ্রাম হতে চলেছে।